[এই লেখায় আমি বাংলাদেশের
কিশোর ও তরুণ বিজ্ঞানপ্রেমীদের সাথে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারে কিছু কথা বলতে
চাই। এই কথাগুলি হয়তো তাদের ভবিষ্যতের বিজ্ঞানচর্চায় কাজে লাগবে। যে পাঠকদের উদ্দেশ্যে
আমি এই কথাগুলি বলছি তারা বয়সে আমার কনিষ্ঠ, তাই তাদের তুমি করে সম্বোধন করছি।]
তুমি যখন এই লেখাটি পড়ছো, আমি ধরে নিচ্ছি তুমি বিজ্ঞান ভালোবাসো,
বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা করো। ভবিষ্যতে তুমি কী হবে, তোমার পেশা কী হবে, কীভাবে কাটবে তোমার
দিনরাত সে সম্পর্কে এখনই তুমি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছো না। কেউই পারে না। কিন্তু
তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছো কিছু একটা হবার। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তুমি
এমনভাবে লেখাপড়া করছো – যেন এই লেখাপড়াটা তোমার স্বপ্ন সফল করে তোলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা রাখে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, লেখক, বিসিএস ক্যাডার, পুলিশ, রাজনীতিবিদ
– যা-ই তুমি হও না কেন, তুমি যেহেতু বিজ্ঞান ভালোবাসো, বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম সম্পর্কে
চিন্তাভাবনা করতে ভালোবাসো – বিজ্ঞানী হবার প্রাথমিক দুটো শর্ত তুমি ইতোমধ্যেই পূরণ
করে ফেলেছো।
তবে বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র ভালোবাসলেই বিজ্ঞানী হওয়া যায় না।
তার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়। বিজ্ঞান অত্যন্ত জটিল বিষয়, বিজ্ঞানের পথ বড় কঠিন
পথ। তুমি হয়তো খেয়াল করেছো বিজ্ঞানচিন্তার পাতায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল বিষয় আমরা
সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি। সেগুলি পড়ার সময় তোমার মনে হতে পারে এ-তো সহজ জিনিস। হ্যাঁ,
ঠিকমতো বুঝতে পারলে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি খুবই সহজ। কিন্তু সেই তত্ত্বগুলি আবিষ্কার
করেছেন যেসব বিজ্ঞানী – তাঁদের আবিষ্কারের পথ অত সহজ নয়। তুমি যখন বিজ্ঞানের কোন একটা
বিষয় – যা সহজভাবে তোমার বোধগম্য আকারে লেখা হয়েছে – পড়ার পর বেশ বুঝতে পারছো, তোমার
ভালো লাগছে, বিজ্ঞানের প্রতি তোমার ভালোবাসা তৈরি হচ্ছে – সেটা হলো ব্যবহারকারির দৃষ্টিতে
বিজ্ঞান, ইংরেজিতে যাকে বলে ইউজার লেভেল সায়েন্স। এই পর্যায়ে বিজ্ঞানের প্রতি তোমার
যে ভালো লাগা তৈরি হয়েছে, বিজ্ঞানী হতে গেলে তাকে আরো অনেক বছর ধরে অনেক দূর নিয়ে যেতে
হবে। তুমি যদি স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী
হও, ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের গবেষক হতে চাও, বিজ্ঞানী হতে চাও – তোমাকে শুধুমাত্র ভালোবাসলেই
হবে না – বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার কঠিন পথটিকেও আপন করে নিতে হবে।
ধরা যাক, তুমি বিজ্ঞানের কঠিন পথ পেরিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা
করতে করতে বিজ্ঞানী হতে চাও। কিন্তু কীভাবে বুঝবে কোন্ পথটি তোমার জন্য সঠিক পথ? কোন্
পথে গেলে তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কোন সহজ সঠিক
উপায় নেই। কিন্তু তোমার যদি বিজ্ঞানের জগৎ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা থাকে এবং এই জগতে
প্রবেশ করার পূর্বপ্রস্তুতি থাকে – তাহলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে কোন্ পথে হাঁটতে
তোমার ভালোও লাগছে, আবার লক্ষ্যেও পৌঁছাতে পারছো।
ইউনেসকোর ইন্সটিটিউট অব স্ট্যাটিসটিক্স এ প্রকাশিত পরিসংখ্যান
[১] থেকে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর মোট বিজ্ঞানীর সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৮৮ লক্ষ। এখানে
আমাদের জেনে রাখতে হবে বিজ্ঞানী আমরা কাদেরকে বলছি। বিজ্ঞান বিষয়ে যারা পড়াশোনা শেষ
করেছেন তাদের সবাই কিন্তু বিজ্ঞানী নন। পৃথিবীর মোট এক কোটি সাতাশ লক্ষ এমবিবিএস ডাক্তার
এবং দুই কোটি সত্তর লক্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার – যারা তাঁদের রুটিনমাফিক পেশাগত দায়িত্ব
পালন করছেন তাঁদেরও সবাই কিন্তু বিজ্ঞানী নন। বিজ্ঞান শিক্ষকদের মধ্যেও যাঁরা শুধুমাত্র
ক্লাসরুমে পড়াচ্ছেন বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছেন – তাঁরাও বিজ্ঞানী নন। বিজ্ঞানী
তাঁরাই – যারা বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করছেন, বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করছেন,
বিজ্ঞান গবেষণা যাঁদের নিয়মিত কর্মজীবনের অংশ। বিজ্ঞানের যেকোনো শাখায় কর্মরত যে কেউই
বিজ্ঞানী হতে পারেন যদি তিনি নিয়মিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন।
জনসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞানী আছেন ইসরায়েলে। সেখানে
প্রতি দশ লক্ষ জনসাধারণের মধ্যে প্রায় সাড়ে নয় হাজার বিজ্ঞানী। তার ঠিক পরেই আছে দক্ষিণ
কোরিয়া (প্রতি মিলিয়নে সাড়ে আট হাজার বিজ্ঞানী।) জাপানে বিজ্ঞানীর সংখ্যা প্রতি মিলিয়নে
সাত হাজার। আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়ায় বিজ্ঞানীর সংখ্যা প্রতি মিলিয়নে
প্রায় সাড়ে চার হাজার। চীনে প্রতি মিলিয়নে আনুমানিক দুই হাজার। ভারতে প্রতি মিলিয়নে
মাত্র তিন শ জন। আমাদের বাংলাদেশে বিজ্ঞানীর সংখ্যা আরো অনেক কম, প্রতি মিলিয়নে মাত্র
একশ জন। সতের কোটি জনসাধারণের এই দেশে বিজ্ঞানীর সংখ্যা মাত্র সতের হাজার। দশ হাজার
মানুষের বিপরীতে আমাদের দেশে আছেন মাত্র একজন বিজ্ঞানী।
এই সীমাহীন বৈষম্যের কারণ কী? বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে বাৎসরিক
বাজেটের কী পরিমাণ বরাদ্দ করা হয় সেটা অবশ্যই একটি বড় ফ্যাক্টর। বৈজ্ঞানিক গবেষণার
জন্য ইসরায়েলে বাৎসরিক বাজেটের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ বরাদ্দ করা হয়। সেটা আমেরিকায় ২.৮৪
শতাংশ, জার্মানিতে ৩.১ শতাংশ, জাপানে ৩.২৬ শতাংশ, চীনে ২.১৯ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায়
৪.৫৩ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় ১.৮৭ শতাংশ, ভারতে ০.৬৫ শতাংশ। বাংলাদেশে বার্ষিক বাজেটে
বিজ্ঞান গবেষণার জন্য আলাদা বাজেট থাকে না বললেই চলে। যা থাকে তাও চলে যায় বৈজ্ঞানিক
কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের পেছনে।
শুধুমাত্র বাজেট বরাদ্দ কম থাকার কারণেই যে আমাদের বিজ্ঞান
গবেষণা পিছিয়ে আছে তা নয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই রয়ে গেছে বিজ্ঞানী তৈরি হবার
সবচেয়ে বড় বাধা। মনে করো তুমি এখন ক্লাস নাইনে পড়ছো, পদার্থবিজ্ঞান তোমার ভালো লাগে,
ভবিষ্যতে তুমি পদার্থবিজ্ঞানী হতে চাও। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানী কীভাবে হতে হয় সে সম্পর্কে
তোমার কোন ধারণা নেই। তোমার স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা তোমাকে হয়তো কখনোই বলেননি যে পদার্থবিজ্ঞানী
হতে গেলে তোমাকে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।
আমাদের বাংলাদেশে সত্যিকারের বিজ্ঞানজগত সম্পর্কে জানা কিংবা
ধারণা লাভ করার তেমন কোনো সহজ উপায় নেই যেখান থেকে তুমি পূর্বপ্রস্তুতি নিতে পারবে।
তোমাদের স্কুলের বিজ্ঞান বইতে যেসব বিষয় লেখা আছে, তোমাদের শিক্ষকরা তোমাদের বাধ্য
করে সেসব যেভাবে লেখা আছে সেভাবে মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য। তোমরাও বাধ্য
হয়ে তাই করো – নইলে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া যায় না। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার
লক্ষ্যে স্কুল-কলেজের পাশাপাশি তোমরা কোচিংও করো যেখানে শেখানো হয় পরীক্ষার প্রশ্নের
উত্তর কীভাবে লিখলে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে। বিজ্ঞান শাখায় এসএসসি ও এইচএসসিতে তোমরা বাধ্যতামূলকভাবে পদার্থবিজ্ঞান,
রসায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, গণিত, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পড়ে থাকো। পড়ার চাপ এত বেশি থাকে
যে এই বিষয়গুলির প্রতি তোমাদের ভালোবাসা জন্মানোর কোন সুযোগই তৈরি হয় না। বরং একটু
এদিক-ওদিক হলেই নম্বর কম পাওয়ার ভয় থেকে তৈরি হয় প্রচন্ড স্নায়ুচাপ। এইচএসসি পরীক্ষা
শেষ হতে না হতেই শুরু হয় তোমাদের ভর্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি।
যারা ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পায়, তারা ডাক্তার হয়ে হাসপাতাল-চেম্বার
করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দেয়। অনেকেই এফসিপিএস, এমডি, এমআরসিপি ইত্যাদি আরো উচ্চতর ডাক্তারি
ডিগ্রি পাস করে। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের সত্যিকারের গবেষণা করার সুযোগ, সময় এবং ইচ্ছে
খুব কম ডাক্তারেরই থাকে।
যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পায়, তাদের হাতেকলমে প্রকৌশল
বিদ্যা শেখার সুযোগ হয়। কিন্তু সিলেবাসের বাইরে তাদের গবেষণা এবং উদ্ভাবনেরও কিছু সুযোগ
থাকে। কিন্তু পাস করে বের হবার পর কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ইঞ্জিনিয়ারই ইঞ্জিনিয়ারিং
এর পরিবর্তে বিসিএস পাস করে প্রশাসক হবার প্রতি বেশি আগ্রহী হয়। আমাদের দেশে উন্নত
প্রযুক্তি নির্ভর কলকারখানা খুব একটা নেই। ফলে আমাদের দেশের সব ইঞ্জিনিয়ারের উপযুক্ত
কাজ করার সুযোগ থাকে না। তাই অনেকেই বিদেশে চলে যায়। বিদেশী কোন ডিগ্রি নিয়ে বিদেশেই
থেকে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিজ্ঞানী হবার সুযোগ পায়।
ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের পর যারা বাকি থাকে – তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে
বিজ্ঞানের যেকোনো শাখায় অনার্স ক্লাসে ভর্তি হয়। কোন্ বিষয়ে পড়তে আগ্রহী হবে সেটা
ঠিক করতে গিয়েও অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে তো তোমরা
জানতেই পারো না কোন্ বিভাগে কী পড়ানো হয়, কোন্ বিষয়ে পাস করলে ভবিষ্যতে কী কী করা
যাবে। কিংবা তুমি যদি ভবিষ্যতে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী হতে চাও – স্কুল থেকেই তোমার
কী কী বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
খুবই কম। বিজ্ঞানীর সংখ্যাও কম। তাই তোমাদের তেমন কোন সুযোগই থাকে না সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের
সাথে কথা বলার বা তাদের কাজকর্ম কাছ থেকে দেখার। আমাদের দেশে কোনো বৈজ্ঞানিক জাদুঘরও
নেই – যেখানে গিয়ে তোমরা বিজ্ঞান শিখতে পারবে।
কিন্তু পৃথিবীর উন্নত দেশে, যেখানে বিজ্ঞানীর সংখ্যা অনেক
বেশি – সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মতো নয়। পৃথিবীর সব উন্নত
দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী
থেকে বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার সবগুলি ধাপে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকে।
আমেরিকার কথা ধরা যাক। সেখানে স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য একেবারে নিচের ক্লাস থেকেই
বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান প্রকল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সারা দেশ থেকে বাছাই
করা সেরা প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রতি যাদের আগ্রহ আছে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা করা হয়। একেবারে প্রাইমারি স্কুলে থাকতেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেসব বিজ্ঞানী
কাজ করছেন – তাদেরকে মাঝে মাঝে স্কুলে নিয়ে এস পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। স্কুলের শিক্ষার্থীদের
মাঝে মাঝে নিয়ে যাওয়া হয় গবেষণাগারে – সেখানে তারা নিজের চোখে দেখতে পারে কীভাবে বৈজ্ঞানিক
গবেষণা করা হয়, কীভাবে বিজ্ঞানীরা কাজ করেন। হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার
মাধ্যমে সত্যিকারের বিজ্ঞান-প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। নাসার মতো প্রতিষ্ঠানের
বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ থাকে শিক্ষার্থীদের। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা
করার সময় থেকেই শুরু হয় সত্যিকারের বিজ্ঞান গবেষণা। শুধুমাত্র বই পড়ে মুখস্থ করে পরীক্ষা
দিয়ে পাস করার উপরই সব গুরুত্ব সেখানে দেয়া হয় না। যারা শুধুমাত্র চাকরি করে টাকা উপার্জন
করার জন্য উদ্দেশ্যে ভর্তি হয়, তাদের কোর্স আর গবেষণা করতে যারা আগ্রহী তাদের কোর্স
আলাদা। উন্নত দেশে বিজ্ঞানী তৈরি করার সুব্যবস্থা আছে।
বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাজগৎ এবং কর্মজগৎ যে অবস্থায় আছে,
সেখান থেকে বিজ্ঞানী হয়ে ওঠা দুঃসাধ্য বটে, তবে অসাধ্য নয়। তুমি যদি সত্যিকারের বিজ্ঞানী
হতে চাও, তাহলে আমাদের দেশ থেকেও বিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব। তারজন্য তোমাকে সেভাবে প্রস্তুতি
নিতে হবে স্কুল-কলেজ থেকেই। তুমি যদি ডাক্তার হও- চিকিৎসাবিজ্ঞানী হতে তোমার কোনো বাধা
নেই। বরং আমাদের দেশে রোগ এবং রোগীর সংখ্যা এত বেশি যে তোমার যদি গবেষণার প্রতি আগ্রহ
থাকে – তুমি অনেক বেশি সুযোগ পাবে এখানে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হবার। তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ার
হও এবং নতুন উদ্ভাবনের প্রতি আগ্রহ থাকে – তাহলে তুমি আমাদের দেশের অনেক কারিগরী সমস্যার
সমাধান করে ফেলতে পারবে। আর যদি তুমি মৌলিক বিজ্ঞান – পদার্থবিজ্ঞন, রসায়ন, জীববিজ্ঞানের
যে কোনো শাখায় গবেষণা করতে চাও – তাহলেও অনেক অনেক কিছু করা সম্ভব।
বিজ্ঞানের যেকোনো শাখাতেই যদি তোমার গবেষণা করার ইচ্ছে থাকে
– তাহলে একটা বিষয় তোমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে। সেটা হলো – বিজ্ঞান গবেষণায় কোনো শর্টকাট
রাস্তা নেই। সেখানে কোনো ধরনের জোড়াতালি চলে না, কোনো ধরনের প্রতারণা বা মিথ্যার স্থান
নেই। বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফল একটুও এদিক-ওদিক করার সুযোগ নেই। যদি কেউ করে – সেটা কারো
না কারো কাছে ধরা পড়বেই। বিজ্ঞান গবেষণা সর্বজনীন। অর্থাৎ বাংলাদেশে বসে কোনো গবেষণার
যে ফল তুমি পাবে, পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় একই বৈজ্ঞানিক পরিবেশে একই ফলাফল পাবে। বিজ্ঞানের
গবেষণায় ভুল করলে ভুল স্বীকার করার মধ্যে কোনো ভয় বা লজ্জা নেই। ভুল করতে করতেই বিজ্ঞানীরা
শিখতে থাকে।
বিজ্ঞানী হবার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো প্রশ্ন করতে শেখা।
বিজ্ঞানে বিনাপ্রশ্নে কোনো কিছুই মেনে নেয়ার সুযোগ নেই। বিজ্ঞানীর কাজ হলো অজানাকে
জানা। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, তার ফলাফল কী হবে তা আগে থেকে জানেন
না। এই অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁদের বিজ্ঞানী করে তোলে।
তাহলে তুমি কীভাবে এগোবে? বিজ্ঞানের যা-কিছু পড়বে – অবশ্যই
ভালোভাবে বুঝতে হবে। শুধু নিজে বুঝলে হবে না, অন্যকেও বোঝানোর দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
তুমি যদি নিজে কোনো কিছু বোঝো, তুমি দেখবে অন্য কাউকে যদি সেটা নিজের মতো করে বোঝাতে
পারো – তাহলে তোমার নিজের কাছেও ব্যাপারটি আরো অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি যে বিষয়ে
বিজ্ঞানী হতে চাও- সেই বিষয়ের শিক্ষকদের সাথে কথা বলে তোমার আগ্রহের কথা জানাও। শিক্ষকরা
আগ্রহী শিক্ষার্থী পেলে ভীষণ আনন্দিত হবেন। দরকার হলে নিজের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষকদের সাথে কথা বলো। কোনো বিষয়ে ভর্তি হবার আগে সেই বিভাগের শিক্ষকদের সাথে কথা
বলা সম্ভব না হলে, শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলো। তোমার যদি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ
থাকে – ইন্টারনেট থেকে এখন সব ধরনের গবেষণা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া যায়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন
বিষয়ে অলিম্পিয়াডসহ আরো অনেক প্রতিযোগিতা হয়। সেগুলিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করো। বিজ্ঞান
বোঝার ক্ষেত্রে নিজের দুর্বলতা কোথায় সেটা খুঁজে বের করো। কোনো কিছু না বুঝলে তাতে
লজ্জার কিছু নেই। বরং না বুঝে মুখস্থ করার চেয়ে কী বুঝতে পারছো না সেটা বের করতে পারাটা
অনেক বেশি দরকারি। বিশ্বমানের বিজ্ঞানীদের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ হয়তো আমাদের
নেই, কিন্তু তাঁদের বৈজ্ঞানিক জীবন নিয়ে লেখা বইগুলি যদি পড়ো – তাহলেও জানতে পারবে
তাঁরা কীভাবে গবেষণা করতেন।
 |
| আইরিন কুরি - কিশোর বয়সেই বিজ্ঞানগবেষণা শুরু করেছিলেন তাঁর মা মেরি কুরির সাহচর্যে |
আগামী এক দশকে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক গবেষণার সুযোগ তৈরি হবে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সমস্যার সমাধানে অনেক নতুন গবেষণা উন্মুক্ত হবে। মহাকাশ গবেষণায় ব্যাপক পরিবর্তন হবে। বায়োটেকনোলজি আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার বিশাল সুযোগ তৈরি হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সাথে খাপ-খাইয়ে চলার প্রযুক্তির গবেষণার অসীম সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ন্যানোমেডিসিন আর ন্যানোটেকনোলজি, প্রাণ রসায়ন এবং নতুন ওষুধ উদ্ভাবন – এরকম হাজার হাজার প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানীর দরকার আমাদের দেশে। যদি বিজ্ঞানী হতে চাও – নিজেকে তৈরি করতে থাকো, তুমি সফল হবেই।
তথ্যসূত্র
১। ইউনেস্কো সায়েন্স রিপোর্ট, প্যারিস, ২০২১।
-----------------------
মাসিক বিজ্ঞানচিন্তার শততম সংখ্যায় প্রকাশিত




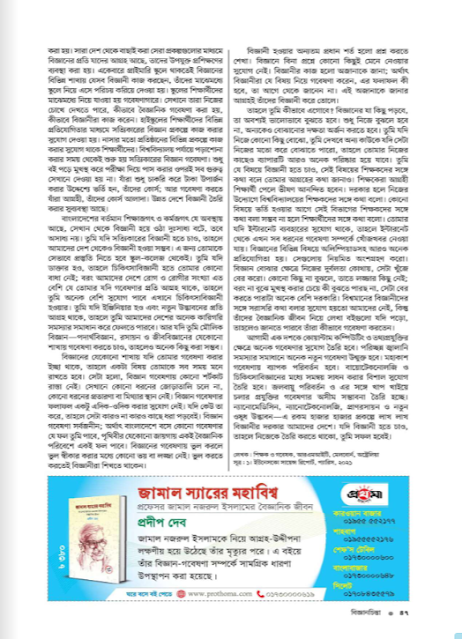




No comments:
Post a Comment