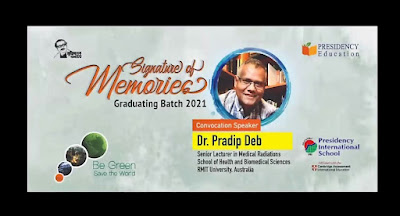বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার
ও উদ্ভাবনের দিক বিবেচনা করলে মানুষ এখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। মহাবিশ্বের কোটি কোটি
আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্যালাক্সির নক্ষত্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে শক্তিশালী টেলিস্কোপের
সাহায্যে। পৃথিবীতে বসে মঙ্গলগ্রহে পাঠিয়ে দিয়েছে স্বয়ংক্রিয় রোবট – ভবিষ্যতের মানুষদের
জন্য বাসযোগ্য নতুন পৃথিবী খুঁজতে। মহাবিশ্বের বিস্ময়কর রহস্যের আবরণ সরাতে শুরু করেছে
মানুষ কয়েক শ’ বছর আগে থেকেই। অথচ মানুষ এখনো নিজের শরীরের সবগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের
কাজকর্ম কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তার পূঙ্খানুপুঙ্খ হদিস পায়নি। যে মহাবিশ্বে আমাদের বাস,
সেই জটিল মহাবিশ্বের মতো জটিলতা রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্কে। সেই কারণেই আমাদের
মস্তিষ্ককে বলা হয় থ্রি পাউন্ড ইউনিভার্স বা চৌদ্দ শ গ্রাম ভরের মহাবিশ্ব।
আমাদের শরীর
ও মনের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মস্তিষ্ক। মানুষের মস্তিষ্কের গড় ভর এক
কেজি চার শ গ্রামের মতো। ছোট্ট একটা ফুলকপির সাইজের মস্তিষ্ক আমাদের। তবে ফুলকপির মতো
অত শক্ত নয়। আমাদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত নরম। তার ভরের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ হলো পানি,
আর বাকিটা চর্বি ও প্রোটিন। কী আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের সমস্ত অনুভূতি
নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মস্তিষ্কের নিজের কোন অনুভূতি নেই। মাথাব্যথা বলতে আমরা যা বুঝি
– তা মস্তিষ্কের ভেতরের ব্যথা নয়।
মস্তিষ্ক আমাদের
শরীরের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির মারাত্মক ক্ষতি হবার পরেও
মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কের কার্যাবলি যদি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় –
তখন শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মস্তিষ্ক তাই প্রাকৃতিকভাবেই
খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। চুল আর ত্বকের পরেই আছে অত্যন্ত শক্ত মাথার খুলি। শরীরের
সবচেয়ে শক্ত হাড়্গুলির একটি হলো মাথার খুলি। এটা আমাদের প্রাকৃতিক হেলমেট। মাথার খুলির
নিচে আছে আরো তিনটি পাতলা অথচ অত্যন্ত শক্ত স্তরের
সুরক্ষা ব্যবস্থা – মেনিঞ্জিস। মেনিঞ্জিসের নিচে আছে বিশেষ এক ধরনের তরল – সেরিব্রোস্পাইনাল
ফ্লুইড। এই তরল নরম মস্তিষ্ককে মাথার খুলির ভেতর নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিকমতো বসিয়ে রাখে,
শরীরের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাথে মস্তিষ্কের সংযোগ স্থাপন করে, রক্ত থেকে মস্তিষ্কের
জন্য দরকারি পুষ্টি জোগায়, এবং মস্তিষ্কের ভেতর কোন বর্জ্য জমলে তা বের করে দেয়।
আমাদের মস্তিষ্কের
কাজকর্ম যেভাবে চলে, তাকে মোটামুটিভাবে একটি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সুপার কম্পিউটারের
সাথে তুলনা করা যায়। আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা কত বেশি তা একটি ছোট্ট উদাহরণ থেকেই
আন্দাজ করা যায়। হাবল স্পেস টেলিস্কোপ গত তিরিশ বছর ধরে যত উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে পেরেছে
– আমাদের মস্তিষ্ক তিরিশ সেকেন্ড সময়ের ভেতর এর চেয়ে অনেক বেশি উপাত্ত বিশ্লেষণ করে।
আমাদের মস্তিষ্কের উপরিভাগের পাতলা কর্টেক্সের ছোট্ট একটা বালুকণার সমান আয়তনে প্রায়
দুই হাজার টেরাবাইট তথ্য ধারণ করতে পারে। তার মানে এপর্যন্ত পৃথিবীতে যে পরিমাণ ডিজিটাল
ডাটা তৈরি হয়েছে তার সবকিছুই আমাদের একটি মস্তিষ্কে ধরে যাবে।
আমাদের মস্তিষ্ককে
কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের সাথে তুলনা করা যায়। স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে
যত তথ্য এবং উপাত্ত আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছায় তার প্রসেসিং চলে মস্তিষ্কে। প্রায় দশ
হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) নিউরন আছে সেখানে। এই নিউরনগুলি একে অপরের সাথে এত বেশি জটিল
সংযোগ তৈরি করে কাজ করে যে এই সংযোগের সংখ্যা প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন বা এক কোটি কোটি ছাড়িয়ে
যেতে পারে।
এই নিউরনের
সংযোগগুলিতে অত্যন্ত কম মাত্রায় জৈববিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত হয়। শরীরের জৈব যৌগের ইলেকট্রন
ও আয়ন পর্যায়ের জটিল বিক্রিয়ায় এই তড়িৎপ্রবাহ তৈরি হয়। এর পরিমাণ অত্যন্ত কম ( সর্বমোট
মাত্র কয়েক মিলি-অ্যাম্পিয়ার)। আমাদের সারা শরীরের উৎপাদিত মোট ক্ষমতা মাত্র ১০০ ওয়াটের মতো। কিন্তু এই এক শ ওয়াটের
মধ্যে বিশ ওয়াটই খরচ হয় মস্তিষ্কের কাজে।
আমাদের মস্তিষ্কের
ভর শরীরের মোট ভরের মাত্র দুই শতাংশ, অথচ শরীরের মোট শক্তির বিশ শতাংশই তা খরচ করে
ফেলে। শিশুদের ক্ষেত্রে তা আরো বেশি। সদ্যোজাত শিশুরা শরীরের মোট শক্তির শতকরা ৬৫ থেকে
৭০ ভাগ খরচ করে মস্তিষ্কের কাজে। তাই তারা প্রায় সারাক্ষণই ঘুমাতে থাকে।
মস্তিষ্কের
নিউরনের সংযোগগুলির প্রতিটি জৈব-বৈদ্যুতিক তরঙ্গপ্রবাহের স্পন্দনের স্থায়ীত্ব মাত্র
এক থেকে দুই মিলিসেকেন্ড, কিন্তু এদের গতি অনেক বেশি – ঘন্টায় প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার।
বিজ্ঞানীরা
মস্তিষ্কের জৈব-বৈদ্যুতিক তরঙ্গের প্রবাহ মাপার চেষ্টা করছিলেন অনেক বছর আগে থেকে।
১৮৭৫ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী রিচার্ড ক্যাটন খরগোশ ও বানরের মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ
মাপার চেষ্টা করেছিলেন গ্যালভানোমিটারে সাহায্যে। মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের রেখাচিত্র
– ইলেকট্রোএনসিফ্যালোগ্রাফি বা ইইজি’র উৎপত্তি হয়েছে তখন থেকেই। এনসিফেলন শব্দের অর্থ
ব্রেইন বা মস্তিষ্ক।
অত্যন্ত সংবেদী
গ্যালভানোমিটার ব্যবহার করে মানুষের মস্তিষ্কের প্রথম ইইজি করেন জার্মান স্নায়ুবিজ্ঞানী
হ্যান্স বার্গার ১৯২৪ সালে। তিনিই প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন যে মানুষ যখন ঘুমায় তখন তাদের
মস্তিষ্কের তরঙ্গের কম্পাঙ্ক, জাগ্রত অবস্থার তরঙ্গের কম্পাঙ্কের চেয়ে ভিন্ন। এরপর
মানুষের বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে মস্তিষ্কের তরঙ্গের কম্পাঙ্কের কী ধরনের পরিবর্তন
হয় তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং পদার্থবিজ্ঞানীরা।
 |
| মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ |
কম্পাঙ্ক অনুসারে
মস্তিষ্কের তরঙ্গকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। আমরা যখন গভীর মনযোগ দিয়ে কোন কাজ
করতে থাকি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গের কম্পাঙ্ক অনেক বেড়ে যায়। কম্পাঙ্ক ৩৫ হার্টজের
বেশি হলে তাদেরকে বলা হয় গামা তরঙ্গ। গামা তরঙ্গ হলো মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ক্ষমতার নির্দেশক।
এই সময় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে অনেক ধরনের তরঙ্গের আদান-প্রদান ঘটে।
আমরা যখন স্বাভাবিক
কাজে ব্যস্ত থাকি তখন আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গের কম্পাঙ্ক থাকে ১২ থেকে ৩৫ হার্টজের
মধ্যে। এই কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বলা হয় বিটা তরঙ্গ। আমরা যখন কথাবার্তা বলি, কোন ব্যাপারে
সিদ্ধান্ত নিই, সমস্যার সমাধান করি, লেখাপড়া শিখি – তখন আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গ –
বিটা তরঙ্গ।
বিশ্রামের সময়
আমাদের মস্তিষ্কের কম্পাঙ্ক আরো কমে যায়। তখন কম্পাঙ্ক থাকে ৮ থেকে ১২ হার্টজের মধ্যে।
এই তরঙ্গগুলিকে আলফা তরঙ্গ বলা হয়। মস্তিষ্কের তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আরো কমে গেলে আমাদের
তন্দ্রা আসে।
মস্তিষ্কের
তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ৪ থেকে ৮ হার্টজের মধ্যে হলে তাদের থেটা তরঙ্গ বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন
কাজ যেগুলি আমরা অভ্যাসবশত করি – যেমন দাঁত ব্রাশ করা, গোসল করা, নিজের ঘরের মধ্যে
হাঁটা ইত্যাদির সময় আমাদের মস্তিষ্ক থেটা তরঙ্গে কাজ করে।
আর সবচেয়ে কম
কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বলা হয় ডেল্টা তরঙ্গ। ডেল্টা তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ০.৫ থেকে ৪ হার্টজ।
এই তরঙ্গে আমাদের মস্তিষ্ক ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য মস্তিষ্কের
এই বিশ্রাম দরকার হয়। ডেল্টা তরঙ্গ হলো মস্তিষ্কের বিশ্রামের তরঙ্গ।
স্নায়ুর চিকিৎসায়
ইইজি প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯৩৭ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে। তারপর
থেকে ইইজি সিস্টেমের অনেক উন্নতি হয়েছে। কম্পিউটার টেকনোলজি এবং ইলেকট্রনিক্সের উন্নতির
সাথে সাথে ইইজি’র ব্যবহারিক ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। মস্তিষ্কের অনেক জটিল রোগ নির্ণয়ে
এবং অন্যান্য চিকিৎসায় রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণে এই ইইজি’র সাহায্যে মস্তিষ্কের তরঙ্গের
পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। রোগী যদি কোমায় চলে যায়, তখন রোগীর মস্তিষ্কের কাজকর্মের
কোন উন্নতি হচ্ছে কি না দেখা হয় মস্তিষ্কের তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে। মাথায় আঘাত পেলে,
কিংবা স্ট্রোক হলে মস্তিষ্কের তরঙ্গের পরিবর্তন হতে পারে। অনিদ্রা, মৃগীরোগসহ অন্যান্য
স্নায়বিক রোগের চিকিৎসায় ভূমিকা রাখছে মস্তিষ্কের তরঙ্গের বিন্যাস।
মস্তিষ্কের
তরঙ্গকে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হলেও – প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কের তরঙ্গ কিন্তু
স্বতন্ত্র। এখানেই মানুষের সাথে রোবটের পার্থক্য। প্রত্যেক মানুষের মৌলিক শারীরিক গঠন
একই রকম হলেও, প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা। তাদের চিন্তার ধরন আলাদা, একই ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ
করে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারটা
মস্তিষ্কের তরঙ্গের মাধ্যমে আলাদা করা যায়, কিন্তু এর সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো সঠিকভাবে
নির্ণয় করা যায়নি। এখানেই মস্তিষ্কের বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।
_____________________
তথ্যসূত্র:
বিল ব্রাইসনের ‘দি বডি এ গাইড ফর অকুপ্যান্টস’, ব্রায়ান ক্লেগের ‘দি ইউনিভার্স ইনসাইড
ইউ’, অনিল শেঠ সম্পাদিত ‘থার্টি সেকেন্ড ব্রেইন’, ক্লিফোর্ড পিকোভারের ‘দি মেডিকেল
বুক’।
______________
বিজ্ঞানচিন্তা জুলাই ২০২১ সংখ্যায় প্রকাশিত